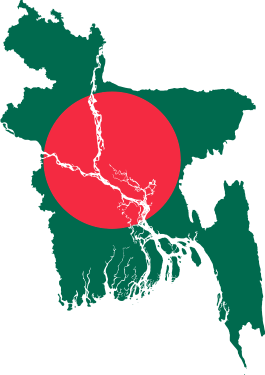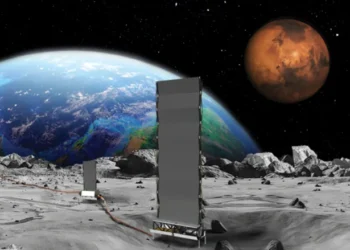প্রথম পর্ব

আমার সোনার বাংলা’ গানের রচনাকাল হিশেবে ১৯০৫ সালই সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। তবে, গানটি যে ১৯০৫ সালেই রচিত হয়েছে, এ-ব্যাপারে অকাট্য প্রমাণ নেই। কেননা গানটির পাণ্ডুলিপি খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাই, রচনাকালও আনুমানিক। এই গান ১৯০৫-এর কিছুকাল আগেও রচিত হয়ে থাকতে পারে। ব্রিটিশ ভারতে প্রথম বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল ঐ বছরের ১৬ অক্টোবর। আর কোলকাতা টাউন হলে এই গান গাওয়া হয়েছিল আগস্টের ৭ বা ২৫ তারিখে।
একেক জায়গায় একেক তারিখ পাওয়া যায়। গানটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষিতেই লিখেছিলেন, এর কোনো নিশ্চয়তা নেই। তবে, কোলকাতা টাউন হলে গানটি প্রথমবার গাওয়ার নেপথ্য উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গভঙ্গ-রদ— এটুকু সর্বজনস্বীকৃত।
রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গের পক্ষে ছিলেন না। তিনি অখণ্ড বঙ্গ চেয়েছিলেন। কোথাও-কোথাও তথ্য দেখা যায়— বঙ্গভঙ্গের ফলে যে দুই বঙ্গ আলাদা হয়েছিল, পিছিয়ে-পড়া মুসলমানজনগোষ্ঠী এতে চাকরিবাকরি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে উপকৃত হচ্ছিল। আবার, এও দেখা যায় যে, বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ববঙ্গ আলাদা কোনো রাজ্য হয়নি, বরং আসামকেও এর সাথে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। মুসলমানদের একাংশ বিশ্বাস করে— বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা যারা করেছিলেন, তারা পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের উন্নতি বরদাশত করতে পারেননি। আবার বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেছিলেন যারা, তাদের কারো-কারো ভাষ্য হলো— বঙ্গভঙ্গের ফলে ‘পূর্ববঙ্গ ও আসাম’ প্রদেশে বাঙালিরা অনেকটা সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছিল। বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতাকারীরা এটিকে মেনে নিতে পারেননি। তারা এটিকে ব্রিটিশদের ‘ডিভাইড অ্যান্ড রুল’ ষড়যন্ত্র হিশেবেও আখ্যায়িত করেন।
এই বিরোধিতার পেছনে আরো অনেক কারণ জড়িত, যা এই লেখার আলোচ্য বিষয়বস্তু না। মোদ্দা কথা— বঙ্গভঙ্গের সাথে বা বঙ্গভঙ্গ রদের সাথে ধর্মের চেয়ে রাজনীতি ও অর্থনীতিই বেশি জড়িত। রদের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বাঙালি জাতীয়তাবাদ। ফলে, নিঃসন্দেহে বলা যায়— ‘আমার সোনার বাংলা’ গানের সাথে বাঙালি জাতীয়তাবাদ ওতপ্রোতভাবে জড়িত।
‘আমার সোনার বাংলা’ বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। তবে, গানটিকে আচমকা আসমানি আঘাতের মতো রাতারাতি এ-দেশের জাতীয় সংগীত বানানো হয়নি। বরং ইতিহাসের বহু স্তর ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে এই গান বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হয়েছে।
একটি নির্দিষ্ট আন্দোলনে ব্যবহৃত হয়ে যাওয়ার পরপরই সেই গানের আবেদন বা মেয়াদকাল শেষ হয়ে যায় না। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে গেছে— এর মানে এই না যে, ১৯১১ সালেই ছয়বছর-বয়স্ক ‘আমার সোনার বাংলা’ গানের অকালমৃত্যু হয়ে গেছে। ‘আমার সোনার বাংলা’ বেঁচে আছে অন্তত একশো উনিশ বছর ধরে।
এ-কথা নিশ্চয়ই সবার জানা— দেশবিভাগের পরপরই পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী একমাত্র উর্দুকে সমগ্র দেশের রাষ্ট্রভাষা হিশেবে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল এবং ১৯৫২ সালে এর প্রেক্ষিতে ভাষা-আন্দোলন হয়েছিল। সেই আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানে উর্দুর বিপরীতে বাঙালি জাতীয়তাবাদের জন্ম দিয়েছিল। তখনকার বাঙালি কবি-সাহিত্যিকরা পূর্ব পাকিস্তানকে ‘পূর্ব পাকিস্তান’ সম্বোধন না-করে ‘পূর্ব বাংলা’ সম্বোধন করতেন। অবিভক্ত পাকিস্তানের রেডিও-টেলিভিশনে রবীন্দ্রনাথ নিষিদ্ধ ছিলেন, সরকারি গণমাধ্যমে কোনো ধরনের রবীন্দ্রসংগীত বাজানো তখন নিষিদ্ধ ছিল, ব্যক্তিপর্যায়েও রবীন্দ্রচর্চা ছিল দুরূহ। কাজী নজরুল ইসলামের সেসব গানই তখন বাজানো হতো, যেগুলো ‘হিন্দুয়ানি না’ কিংবা ‘কম হিন্দুয়ানি’। কথিত ‘হিন্দুয়ানি’ শব্দ সরিয়ে, যেমন ‘সজীব করিব মহাশ্মশান’-কে ‘সজীব করিব গোরস্তান’ বানিয়ে, তৎকালে নজরুলের গানের মুসলমানি করা হয়েছে। বাংলা বাক্য আরবি-ফারসি কিংবা উর্দু হরফে লেখার প্রস্তাব দেওয়ার মতো অকল্পনীয় ধৃষ্টতাও ঐ আমলে দেখানো হয়েছে।
১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময়ে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধ থাকে। ১৯৬৭ সালের ২৩ জুন আইউব খান সরকার রবীন্দ্রসংগীত প্রচারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন বলেছিলেন— ‘রবীন্দ্রসংগীত আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গ নয়।’
১৯৬১ সাল ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবর্ষ। সামরিক শাসকদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে রবীন্দ্রশতবর্ষ উদযাপন তখন অত সহজ কম্ম ছিল না। বিচারপতি মাহবুব মুর্শেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক গোবিন্দ চন্দ্র দেব, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীদের নেতৃত্বে বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা সেই পরিস্থিতিতেও রবীন্দ্রশতবর্ষ উদযাপন করেছিলেন এবং এই অপরাধে শাসকগোষ্ঠীর চক্ষুশূলে পরিণত হয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ করে রাখা অত্যন্ত জরুরি যে, মুক্তিযুদ্ধকালে হত্যা করে গোবিন্দ চন্দ্র ও মোফাজ্জল হায়দারকে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা তাদের সেই অপরাধের শাস্তিও দিয়েছিল। ১৯৬১ সালের রবীন্দ্রশতবর্ষ উদ্যাপন হয়ে উঠেছিল ১৯৭১ সালে তাদের মৃত্যুর কারণ। অর্থাৎ সামরিক শাসকদের রবীন্দ্রভীতি আর বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের রবীন্দ্রপ্রীতি কোনো মামুলি ব্যাপার বা ছেলেখেলা ছিল না, ছিল এক রক্তক্ষয়ী অধ্যায়ের সূচনাপর্ব।
এই রবীন্দ্রনাথের গানই প্রাক-একাত্তরকালে স্বাধীনতাকামী জনতাকে উদ্বেলিত করেছে, একাত্তরে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে উজ্জীবিত করেছে, একাত্তর-পরবর্তীকালে যুগিয়েছে স্বৈরাচারপতনের মন্ত্রণা। অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানিদের উর্দু জাতীয়তাবাদের বিপরীতে পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ব বাংলার বাসিন্দাদের পালটাপালটি বাঙালি জাতীয়তাবাদের অন্যতম নিয়ামক হিশেবে কাজ করেছেন ১৯৪১ সালে মারা যাওয়া রবীন্দ্রনাথ। জীবিত না-থেকেও রবীন্দ্রনাথ পূর্ব পাকিস্তানে জীবিত ছিলেন বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রভাবক হিশেবে।
একষট্টি-পরবর্তীকালে সন্জীদা খাতুনদের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানট, যার সদস্য ছিলেন মূলত একষট্টিতে রবীন্দ্রশতবর্ষ উদ্যাপনের আয়োজকরা। পশ্চিম পাকিস্তানিদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের প্রতিবাদে ১৯৬৭ সালের পহেলা বৈশাখ ভোরে রমনা উদ্যানের অশ্বত্থগাছের পাদদেশে ছায়ানটের জনা বিশেক শিল্পী বসে পড়েছিলেন সেরেফ গান গাওয়ার জন্য। মূলত রবীন্দ্রনাথের গানই ছিল সেই সংগীতায়োজনের উপজীব্য। ও রকম গুমোট পরিস্থিতিতে বন্দুকের নলের মুখে রবীন্দ্রনাথকে উপজীব্য করে প্রকাশ্যে গান গাইতে বসা, উপর্যুপরি বাংলা গান গাইতে থাকা, উর্দু-আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাওয়া নিশ্চয়ই সহজ কোনো কাজ ছিল না। তখন সেরেফ এ-রকম একটা সংগীতায়োজনই ছিল বিশাল রাজনৈতিক প্রতিবাদ।
সম্ভবত ১৯৬৭ সালেই পহেলা বৈশাখকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিশেবে ব্যবহারের সূত্রপাত হয় এবং এই হাতিয়ার ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক স্বৈরশাসকদের বিপক্ষে, এই হাতিয়ার ছিল বাংলার স্বাধিকার আদায়ের পক্ষে, এই হাতিয়ার ছিল বাঙালিদের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানিদের রাজনৈতিক-সামরিক-অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে।
একাত্তরের যুদ্ধ নিছক সামরিক ছিল না। যুদ্ধ পর্যন্ত পৌঁছতে, অর্থাৎ যুদ্ধের প্রেক্ষাপট তৈরি হতে যে সাংস্কৃতিক ধাপগুলো ছিল; এদের মধ্যে এই পহেলা বৈশাখ উদ্যাপনও ছিল অন্যতম।
পূর্ব পাকিস্তানে কৌশলগত পহেলা বৈশাখ উদ্যাপনের সাথে জড়িত প্রয়াত রবীন্দ্রনাথ। শত্রুমুক্ত বাংলাদেশে ‘আমার সোনার বাংলা’ আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় সংগীত হয় ১৯৭২ সালের ১৩ জানুয়ারি। কিন্তু তা শেখ মুজিবুর রহমানের একক পছন্দে হয়নি। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলাদেশ অস্থায়ী সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে ‘আমার সোনার বাংলা’ জাতীয় সংগীত হিশেবে গাওয়া হয়।
মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ এবং স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রেও এই গানকে জাতীয় সংগীত হিশেবেই গাওয়া হতো। আরেকটু পিছিয়ে গেলে, ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ স্বাধীন বাংলা ছাত্রসংগ্রামপরিষদের সভায়ও ‘আমার সোনার বাংলা’ গাওয়া হয় জাতীয় সংগীত হিশেবে। ২৩ মার্চ পাকিস্তানদিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠান থাকলেও ঢাকা টেলিভিশনের বাঙালি কর্মীরা পাকিস্তানদিবসের কোনো অনুষ্ঠান প্রচার করতে দেননি। পাকিস্তানের জাতীয় সংগীতের বদলে এদিন প্রচারিত হয় ‘আমার সোনার বাংলা’। পাকিস্তানের জাতীয় পতাকার বদলে পর্দায় ভেসে উঠেছিল স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা।
১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে শিল্পীরা সমবেত কণ্ঠে পরিবেশন করেন এই গান। ছাত্রলিগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল আলম খান ২ মার্চ ছাত্রলিগ-নেতাদেরকে (আবদুর রাজ্জাক, শেখ ফজলুল হক মণি, তোফায়েল আহমদ, নূরে আলম সিদ্দিকি, আ স ম আবদুর রব, আবদুল কুদ্দুস মাখন ও শাজাহান সিরাজ) নিয়ে তৎকালীন ইকবাল হলের ক্যান্টিনে বৈঠকে বসেছিলেন, সেখানেও প্রস্তাব এসেছিল ‘আমার সোনার বাংলা’-কে জাতীয় সংগীত করার। এর পর ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের জনসভায় স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে ‘আমার সোনার বাংলা’ গানটিকে গ্রহণের ঘোষণা আসে।
১৯৭০ সালে জহির রায়হানের ‘জীবন থেকে নেওয়া’ চলচ্চিত্রেও ‘আমার সোনার বাংলা’ গানটি ব্যবহৃত হয় এবং তুমুল জনপ্রিয় হয়। ১৯৬৬ সালে ঢাকার ইডেন হোটেলে আওয়ামি লিগের তিনদিনব্যাপী কাউন্সিল অধিবেশনেরও উদ্বোধন হয়েছিল ‘আমার সোনার বাংলা’ গাওয়ার মধ্য দিয়ে। ১৯৫৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত সাংসদদের সম্মানে শেখ মুজিব কার্জন হলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গান পরিবেশিত হয়েছিল। ঐ অনুষ্ঠানে সন্জীদা খাতুনকে ‘আমার সোনার বাংলা’ গাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন শেখ মুজিব।
ঢাকা জেলা ছাত্রলিগের সাবেক সভাপতি ‘আবদুল আজিজ বাগমার’ জন্ম দিয়েছিলেন ‘অস্থায়ী পূর্ববঙ্গ সরকার’। সংক্ষেপে ‘অপূর্ব সংসদ’। আরো সংক্ষেপ করে লেখা হতো ‘অপু’। তারা একটি সরকারকাঠামোও ঠিক করেছিলেন। আবদুল আজিজ বাগমাররাও ‘অপু-৩’ ইশতেহারে নতুন দেশের নাম ‘বাংলাদেশ’ এবং জাতীয় সংগীত হিশেবে ‘আমার সোনার বাংলা’ প্রস্তাব করেছিলেন। অর্থাৎ বাংলাদেশের স্বাধীনতা হুট করে ১৯৭১ সালে এসে পড়েনি। এর বহু বছর আগে থেকেই স্বাধীনতার কথা চিন্তাভাবনা করা হচ্ছিল, সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা করা হচ্ছিল এবং নতুন দেশের জাতীয় সংগীতও ভেবে রাখা হয়েছিল। অর্থাৎ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যেমন আচমকা আসেনি, বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতও আচমকা আসেনি। স্বাধীনতা এসেছে পর্যায়ক্রমে এবং সেইসব পর্যায়ের প্রতিটি পর্যায়ে ‘আমার সোনার বাংলা’ গানকেই জাতীয় সংগীত হিশেবে ভেবে রাখা হয়েছে, দেশ স্বাধীন হওয়ার আগেই এই গানকে জাতীয় সংগীতের মর্যাদা দিয়ে গাওয়া হয়েছে, এই গান কাজ করেছে দেশ স্বাধীন করার সাংস্কৃতিক মন্ত্র হিশেবেও।
বাংলাদেশের সম্ভাব্য জাতীয় সংগীত যেহেতু দেশ স্বাধীন হওয়ার আগেই নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে; তাই, এই গানে যুদ্ধের প্রসঙ্গ নেই, শহিদদের উল্লেখ নেই। মোদ্দা কথা— বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং ‘আমার সোনার বাংলা’ গান পরস্পরের সাথে বিচ্ছিন্ন কোনো সত্তা না, এরা বরং একে অন্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এজন্যই, ১৯৭২ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত নির্বাচনের জন্য সরকারকে মোটেই বেগ পেতে হয়নি, জাতীয় সংগীত হিশেবে তখন ‘আমার সোনার বাংলা’ই হয়ে উঠেছিল স্বয়ংক্রিয় পছন্দ।
বাংলাদেশে জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের প্রথম উদ্যোগ এসেছিল খন্দকার মোশতাক আহমেদের হাত ধরে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর মোশতাক রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিলেন তিরাশি দিন। এই ক’দিনেই তিনি বাংলাদেশের জাতীয় স্লোগান ‘জয় বাংলা’ পালটে ‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ’-এর আদলে ‘বাংলাদেশ জিন্দাবাদ’ করেছিলেন, বাংলাদেশ বেতারের নাম ‘রেডিও পাকিস্তান’-এর আদলে ‘রেডিও বাংলাদেশ’ করেছিলেন এবং উদ্যোগ নিয়েছিলেন জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের।
বাংলাদেশের স্বাধীনতার সাথে সম্পৃক্ত সবকিছুকেই বদলে ফেলে তিনি পাকিস্তানি ভাবাদর্শ চালু করতে চেয়েছিলেন এবং এরই অংশস্বরূপ জাতীয় সংগীতেও হাত দিয়েছিলেন। জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের জন্য তিনি উচ্চপর্যায়ের একটি কমিটি গঠন করে দিয়েছিলেন, সেই কমিটির প্রধান করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক কাজী দীন মুহম্মদকে, নির্দেশ দিয়েছিলেন এক মাসের মধ্যে নতুন জাতীয় সংগীত নির্ধারণ করতে। দীন মুহম্মদ কমিটি এ-ব্যাপারে তিনটি বৈঠক করে এবং দুটো গানের যেকোনো একটিকে জাতীয় সংগীত করার প্রস্তাব দেয়— কাজী নজরুল ইসলামের ‘চল চল চল’ এবং ফররুখ আহমদের ‘পাঞ্জেরি’। কিন্তু অভ্যুত্থান-পালটাঅভ্যুত্থানের ডামাডোলে মোশতাক জাতীয় সংগীত পরিবর্তন করে যেতে পারেননি।
উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো— কাজী দীন মুহম্মদ ছিলেন পাকিস্তানের একজন দালাল শিক্ষক। মুক্তিযুদ্ধকালে ‘পূর্ব পাকিস্তান’-এর যে-পাঁচসদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধিদল পশ্চিম পাকিস্তানে রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানের সাথে দেখা করতে গিয়েছিল, দীন মুহম্মদ ছিলেন সেই পাঁচজনের একজন। বাকি চারজন ছিলেন অবজার্ভার গ্রুপ অব পাবলিকেশন্সের মালিক হামিদুল হক চৌধুরী, পাকিস্তানের তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মাহমুদ আলী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সাজ্জাদ হোসেন এবং বিচারপতি নুরুল ইসলাম। মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানের দালালি করার অপরাধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব শিক্ষককে স্বাধীন বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়া হয়েছিল, দীন মুহম্মদ তাদের অন্যতম। দীন মুহম্মদের ব্যাপারে এই তথ্যগুলোর উৎস ‘মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র’ কর্তৃক ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত বই ‘একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়’।
দীন মুহম্মদ যে-ফররুখ আহমদের কবিতাকে জাতীয় সংগীত হিশেবে প্রস্তাব করেছিলেন, মজার ব্যাপার হলো— মুক্তিযুদ্ধকালে সেই ফররুখও পাকিস্তানের দালাল ছিলেন। ১৯৭১ সালের ১৭ মে সংবাদপত্রে যে-পঞ্চান্ন বুদ্ধিজীবী পাকিস্তানের পক্ষে বিবৃতি দিয়েছিলেন; তাদের তালিকার দীন মুহম্মদও আছেন, ফররুখও আছেন। পঞ্চান্নজনের পুরো তালিকা পাওয়া যাবে ঐ একই বইয়ে (একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়)।
১৯৬৭ সালে পাকিস্তানে রবীন্দ্রসংগীত নিষিদ্ধ হওয়ার পর সেই নিষেধাজ্ঞার পক্ষে যে-চল্লিশ বুদ্ধিজীবী বিবৃতি দিয়েছিলেন, ফররুখ তাদেরও একজন। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করে ফররুখ লেখালিখি করেছিলেন বিধায় স্বাধীন দেশে তিনি বেতারের চাকরি খুইয়েছিলেন, যুদ্ধের পর বাংলা অ্যাকাডেমিতে তার প্রবেশ অঘোষিতভাবে নিষিদ্ধ ছিল এবং ১৯৭৪ সালে মৃত্যুর পর তাকে কবরস্থ করার জায়গা নিয়েও জটিলতা দেখা দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত কবি বে-নজীর আহমদ শাহজাহানপুর পারিবারিক কবরস্থানে ফররুখকে কবর দেওয়ার জায়গা করে দেন। উল্লেখ্য, বে-নজীরও স্বাধীনতাবিরোধী ছিলেন।