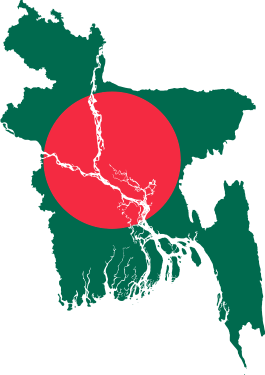২য় ও শেষ পর্ব
 ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের দাবি তোলা হয়েছিল প্রকাশ্যে। ১৯৭৬ সালের ৭ মার্চ সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে তৎকালীন বিমানবাহিনী প্রধান গোলাম তাওয়াব তিনদিনব্যাপী একটি ‘সিরাত মাহফিল’ এর আয়োজন করেছিলেন। তারিখ হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল ৭ মার্চকেই, কারণ পাঁচ বছর আগের এই দিনে শেখ মুজিবুর রহমান একই মাঠে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন। সিরাত মাহফিলে বক্তব্য রাখেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত এবং মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা, যাদের অধিকাংশই বাহাত্তরের দালাল আইনে সাজাপ্রাপ্ত।
১৯৭৬ সালে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের দাবি তোলা হয়েছিল প্রকাশ্যে। ১৯৭৬ সালের ৭ মার্চ সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে তৎকালীন বিমানবাহিনী প্রধান গোলাম তাওয়াব তিনদিনব্যাপী একটি ‘সিরাত মাহফিল’ এর আয়োজন করেছিলেন। তারিখ হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল ৭ মার্চকেই, কারণ পাঁচ বছর আগের এই দিনে শেখ মুজিবুর রহমান একই মাঠে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন। সিরাত মাহফিলে বক্তব্য রাখেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত এবং মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা, যাদের অধিকাংশই বাহাত্তরের দালাল আইনে সাজাপ্রাপ্ত।
বক্তব্য রাখেন তরুণ মওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীও। স্বাধীনতাবিরোধীদেরকে একযোগে মাঠে নামালে মুক্তিযোদ্ধারা কী ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখান, তা পরখ করে দেখাই ছিল ঐ মাহফিল আয়োজনের উদ্দেশ্য। আলোচ্য মাহফিল থেকে দাবি ওঠে জাতীয় সংগীত ও জাতীয় পতাকা পরিবর্তনের, এমনকি বাংলাদেশকে ‘ইসলামি প্রজাতন্ত্র’ ঘোষণারও। সেই মাহফিলে স্লোগান দেওয়া হয়েছিল— ‘তাওয়াব ভাই, তাওয়াব ভাই, চান-তারা পতাকা চাই।’ খালেদা জিয়ার সাবেক প্রেস-সচিব মারুফ কামাল খানের কলাম পড়ে জানলাম— ঐ মাহফিলে, গোলাম আজমের লিখিত বক্তব্যও পড়ে শোনানো হয়েছিল।
১৯৭৮ সালের ১২ ডিসেম্বর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সিনেট অধিবেশনে কোরান তেলাওয়াতের আগে জাতীয় সংগীত গাওয়ায় জিয়াউর রহমানকে চট্টগ্রাম জেলা বিএনপির নেতা ডা. ইউসুফ বলেছিলেন— ‘স্যার, আমাদের পতাকায় ইসলামি রং নেই, এটা আমাদের ভালো লাগে না। এটা ইসলামি তাহজ্জিব ও তমুদ্দুনের সাথে মিলছে না।’ উত্তরে জিয়া বলেছিলেন— ‘হবে, হবে। সবকিছুই হবে। আগে হিন্দুর লেখা জাতীয় সংগীত বদলানো হোক। তারপর জাতীয় পতাকার কথা ভাবব।’ ডা. ইউসুফ ও জিয়াউর রহমানের এই কথোপকথন পেয়েছি সাংবাদিক আবেদ খানের ‘ষড়যন্ত্রের জালে বিপন্ন রাজনীতি’ বইয়ে। তবে, অভিযোগ আছে— সাংবাদিক হিশেবে আবেদ খান আওয়ামি লিগ-অনুগত। তাই, তার বইয়ের বক্তব্য বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করতে হবে নিজদায়িত্বে। আবেদ খান তার বইয়ে কোনো তথ্যসূত্র উল্লেখ করেননি।
ওদিকে ১৯৭৮ সালেরই ৮ মে ইত্তেফাকে প্রকাশিত একটি সাক্ষাৎকারে জিয়াউর রহমানকে প্রশ্ন করা হয়েছিল— ‘জাতীয় সংগীত ও জাতীয় পতাকা বদলানোর ব্যাপারে কোনো-কোনো মহল হইতে দাবি উঠিয়াছে। সে-সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কী?’ এর জবাবে জিয়া বলেছিলেন— ‘এগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা যায় না। এগুলি পারমানেন্সির ভিত্তিতেই গ্রহণ করা হয়।’ জিয়াউর রহমানের আমলে জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হয় এর পরের বছর।
১৯৭৯ সালের ৩০ এপ্রিল জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের প্রস্তাব আসে। ঐ সময়ের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায়, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শাহ্ আজিজুর রহমান এক গোপন চিঠিতে মন্ত্রিপরিষদকে লেখেন— ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা একটি গান বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। তিনি বাংলাদেশের নাগরিক নন। আমার সোনার বাংলা গানটি আমাদের সংস্কৃতির চেতনার পরিপন্থি বিধায় জাতীয় সংগীত পরিবর্তন আবশ্যক।’ ঐ চিঠিতে ‘আমার সোনার বাংলা’র পরিবর্তে ‘প্রথম বাংলাদেশ, আমার শেষ বাংলাদেশ’-কে জাতীয় সংগীত করার প্রস্তাব করেন শাহ্ আজিজ (গীতিকার মনিরুজ্জামান মনির, সুরকার আলাউদ্দিন আলী)।
প্রধানমন্ত্রীর ঐ চিঠি পেয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ রেডিও, টেলিভিশন এবং সব সরকারি অনুষ্ঠানে প্রথম বাংলাদেশ গানটি প্রচারের নির্দেশনাও জারি করে। এ-সময়ে রাষ্ট্রপতির অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীতের পাশাপাশি ‘প্রথম বাংলাদেশ, আমার শেষ বাংলাদেশ’ গাওয়া শুরু হয়। কিন্তু জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের পরিকল্পনা ১৯৮১ সালে জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর থেমে যায়। এই অনুচ্ছেদে ব্যবহৃত তথ্যগুলো নিয়েছি দৈনিক যুগান্তরের ২০১৯ সালের ৭ আগস্টের অনলাইন সংস্করণ থেকে। উল্লেখ্য— মুক্তিযুদ্ধের সক্রিয় বিরোধিতা করার দায়ে শাহ্ আজিজুর রহমান বাহাত্তরের দালাল আইনে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন এবং রাষ্ট্রপতির সাধারণ ক্ষমার আওতায় মুক্তি পেয়েছিলেন। মুক্তি পেয়ে আবারও তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন বলে অভিযোগ ওঠে এবং ১৯৭৫ সালে আবারও গ্রেপ্তার হন।
জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের তোড়জোড় খালেদা জিয়ার আমলেও দেখা গিয়েছিল। ২০০২ সালের ১৯ মার্চ তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী ও জামায়াতে ইসলামির আমির মতিউর রহমান নিজামী এবং সমাজকল্যাণমন্ত্রী ও জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল আলি আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের লক্ষ্যে একটি যৌথ সুপারিশপত্র প্রধানমন্ত্রীর কাছে জমা দেন। তাতে বলা হয়— ‘সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে আমাদের ইসলামি মূল্যবোধ ও চেতনার আলোকে জাতীয় সংগীত সংশোধিত হওয়া প্রয়োজন।’ প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া চিঠিটা প্রত্যাখ্যান না-করে সংস্কৃতিমন্ত্রণালয়ে পাঠান। সংস্কৃতিমন্ত্রী বিষয়টি অতি গুরুত্বপূর্ণ বলে সচিবের কাছে প্রেরণ করেন। জাতীয় সংগীত পরিবর্তনকে সংস্কৃতিমন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারবহির্ভূত বিষয় অভিহিত করে সচিব তা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠান। একই বছরের ১৯ আগস্ট প্রস্তাবটি সংস্কৃতিমন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। কিন্তু সেই সরকারের আমলে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়নি। এই অনুচ্ছেদে ব্যবহৃত তথ্যগুলোও নিয়েছি দৈনিক যুগান্তরের ২০১৯ সালের ৭ আগস্টের অনলাইন সংস্করণ থেকে। উল্লেখ্য— মুক্তিযুদ্ধকালে গণহত্যা সংঘটনে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে সহযোগিতার দায়ে নিজামী-মুজাহিদ উভয়েরই ফাঁসি কার্যকর হয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের দাবি তোলার উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি হলো সংক্ষেপে এই।
হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের আমলেও জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের উদ্যোগের কথা শুনেছি, তবে দালিলিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সাংবাদিকসম্মেলন ডেকে সম্প্রতি একই দাবি তুলেছেন গোলাম আজমের ছেলে আবদুল্লাহিল আমান আজমি। ‘মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস’ তুলে ধরার জন্যও আজমি আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের ‘সঠিক ইতিহাস’-এ বাবা আজমের অবস্থান কী বা কোথায়, পুত্র আজমি তা উল্লেখ করেনি। একই সাংবাদিকসম্মেলনে তিনি তার বাবাকে উলটো ‘সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি’ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। মুক্তিযুদ্ধকালে গোলাম আজম ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামির আমির এবং ছিলেন একাত্তরের গণহত্যার শীর্ষ-কুশীলবদের একজন। গোলাম আজম বাংলাদেশের শুধু জন্মের বিরোধিতা করেছিলেন, তা না। যুদ্ধে পরাজয় আঁচ করতে পেরে একাত্তরের নভেম্বরেই তিনি বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানে পালিয়ে যান। বাংলাদেশের বিরোধিতা তিনি যে কেবল যুদ্ধকালেই করেছিলেন, তা-ও না। যুদ্ধশেষেও তিনি পাকিস্তানে বসে বাংলাদেশবিরোধিতা অব্যাহত রেখেছিলেন। ১৯৭২ সালে পাকিস্তানে গোলাম আজম ‘পূর্ব পাকিস্তান পুনরুদ্ধার সপ্তাহ’ পালন করেন, লন্ডনে গিয়ে ‘পূর্ব পাকিস্তান পুনরুদ্ধার’ কমিটি গঠন করেন। সৌদি আরবে আন্তর্জাতিক যুবসম্মেলনে গিয়ে তিনি মুসলমান-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোকে আহ্বান জানান বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি না-দেওয়ার জন্য এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে কোনো সহযোগিতা না-করার জন্য।
১৯৭৪ সালে পাকিস্তান যখন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়, গোলাম আজম তাতেও বিরোধিতা করেছিলেন। সবকিছুতে ব্যর্থ হয়ে আজম চেষ্টা করেছিলেন দুই দেশকে নিয়ে একটা কনফেডারেশন গড়ে তুলতে। শেষ পর্যন্ত ১৯৭৮ সালে মা মারা যাওয়ার পর জিয়াউর রহমান সরকার গোলাম আজমকে বিনা ভিসায় পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে আসতে দিয়েছিলেন। সেই যে এলেন, তিনি পাকিস্তানে আর ফিরে গেলেন না। পরবর্তী ষোলো বছর তিনি বিদেশী নাগরিক হিশেবে অবৈধভাবে বাংলাদেশে ছিলেন। ১৯৯১ সালের নির্বাচনের পর সরকারগঠনে বিএনপিকে সহযোগিতার পুরষ্কারস্বরূপ ১৯৯৪ সালে আদালতের রায়ের মাধ্যমে গোলাম আজম বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পেয়েছিলেন।
উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে যারা বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের প্রস্তাব করেছিলেন; সামান্য চোখ বোলালেই দেখা যায়— এদের প্রত্যেকেই হয় মুক্তিযুদ্ধবিরোধী বুদ্ধিজীবী অথবা বাহাত্তরের দালাল আদেশে দণ্ডপ্রাপ্ত, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে ফাঁসির আদেশপ্রাপ্ত বা নব্বই বছরের কারাদণ্ডপ্রাপ্ত রাজনৈতিক নেতা কিংবা কোনো যুদ্ধাপরাধীর সন্তান।
এদের সমস্যা কেবল জাতীয় সংগীতে না; জাতীয় পতাকা, জাতীয় স্মৃতিসৌধ, শহিদমিনার, বাংলা বর্ষবরণ— এদের সমস্যা সবকিছুতেই। জাতীয় সংগীতে বা ‘আমার সোনার বাংলা’য় যাদের আপত্তি আছে; স্মৃতিসৌধ বা শহিদমিনারে ফুল দেওয়াও তাদের কাছে হারাম, শিখা চিরন্তনও হারাম, পান্তা-ইলিশও হারাম। অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধ বা বাংলাদেশের জন্মের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট সবকিছুতেই এদের আপত্তি। কারণ শহিদমিনারের ইতিহাস পাকিস্তানরাষ্ট্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার প্রেক্ষাপট তৈরির ইতিহাস, জাতীয় সংগীত ও জাতীয় পতাকার ইতিহাস রেসকোর্স ময়দানে তিরানব্বই হাজার সৈন্যসহ পতিত পাকিস্তানরাষ্ট্রের আত্মসমর্পণের ইতিহাস, জাতীয় স্মৃতিসৌধের সাত স্তম্ভের ইতিহাস স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির সাতটি প্রলয়ঙ্কর পর্বের ইতিহাস (ভাষা-আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, সংবিধান-আন্দোলন, শিক্ষা-আন্দোলন, ছয়দফা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এবং মুক্তিযুদ্ধ)।
একাত্তরে এরাই মুক্তিযোদ্ধাদেরকে গালি দিতেন ‘কাফের-মুরতাদ’ বলে, ডাকতেন ‘বিচ্ছিন্নতাবাদী’ বলে, সাব্যস্ত করতেন ‘রুশ-ভারতের চর’ বলে। একাত্তরের পর এরাই চেষ্টা করেছেন বাংলাদেশের জন্মের সাথে সম্পৃক্ত সবকিছুকে সমূল উৎপাটন করতে। আগেই উল্লেখ করেছি— ‘আমার সোনার বাংলা’ হঠাৎ করে এক রাতের মধ্যে জাতীয় সংগীত হয়ে যায়নি, হয়েছে বছরের পর বছর ধরে ক্রিয়াশীল ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। আবার জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের আওয়াজও হঠাৎ নয়। এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের পর খন্দকার মোশতাকের হাত ধরে, এই আওয়াজের সর্বশেষ প্রতিধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে যুদ্ধাপরাধী গোলাম আজমের পুত্র আবদুল্লাহিল আমান আজমির কণ্ঠে। মধ্যবর্তী ঊনপঞ্চাশ বছরে পাকিস্তানপন্থি বহু বাঙালি বুদ্ধিজীবী জাতীয় সংগীত হিশেবে ‘আমার সোনার বাংলা’-কে বহুভাবে বিতর্কিত করার চেষ্টা করেছেন, ওয়াজ মাহফিলের সিকি-শিক্ষিত বক্তারা এই গানে হিন্দুয়ানি উপকরণ ও শেরেক খুঁজে পেয়েছেন, মাদ্রাসাগুলো বন্ধ রেখেছে ‘আমার সোনার বাংলা’ গাওয়া। মুক্তিযুদ্ধকালে অল্পকিছু বাদে অধিকাংশ মাদ্রাসারও ভূমিকা ছিল পাকিস্তানের পক্ষে। ফলে, এ-কথা আর বলে দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না— জাতীয় সংগীত হিসেবে ‘আমার সোনার বাংলা’ যাদের পছন্দ না; তারা কারা, তাদের উদ্দেশ্য কী, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ প্রশ্নে তাদের অবস্থান কী।
রবীন্দ্রবিরোধীদের কেউ-কেউ বলছেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ‘ধনধান্য পুষ্পভরা’ বা কাজী নজরুল ইসলামের ‘চল চল চল’ গানকে জাতীয় সংগীত করতে। কিন্তু যেসব অভিযোগ ‘আমার সোনার বাংলা’র বিরুদ্ধে আছে, এই দুই গানও তা থেকে মুক্ত না। ‘ধনধান্য পুষ্পভরা’র একটি বাক্য— ‘ও মা, তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি।’ চাইলে দ্বিজেন্দ্রলালের এই ‘মা’-কে ‘মা কালী’ আখ্যা দিয়ে এই গানেও হিন্দুত্ব বা শেরেক খোঁজা যায়, একই জিনিশ খোঁজা যায় নজরুলের ‘চল চল চল’ গানের ‘সজীব করিব মহাশ্মশান’ বাক্যেও। তদুপরি দ্বিজেন্দ্রলাল আবার অমুসলমান। ওদিকে দ্বিজেন্দ্রলাল-নজরুল কারো জন্মই বাংলাদেশে না, দুজনেরই জন্মস্থান রবীন্দ্রনাথের রাজ্যে। এর ওপর নজরুল আবার হিন্দুদের শ্যামাসংগীতও লিখে বসে আছেন, ভগবান-বুকে পদচিহ্ন আঁকতে চেয়েছেন, মসজিদের তালা ভাঙতে চেয়েছেন, ছেলের নাম রেখে বসে আছেন কৃষ্ণ মোহাম্মদ। কারো-কারো অভিযোগ— ‘আমার সোনার বাংলা’ গানে সরাসরি ‘বাংলাদেশ’ শব্দটি নেই, বাংলাদেশের অবাঙালি আদিবাসীদের উল্লেখ নেই। ঘটনা হলো— ‘বাংলাদেশ’ শব্দ ‘ধনধান্য পুষ্পভরায়’ও নেই, ‘চল চল চল’ গানেও নেই। আর একইসাথে বাঙালি-অবাঙালি সবার কথা উল্লেখ আছে, এমন কোনো গান অদ্যাবধি রচিত হয়নি; যা দেশের জাতীয় সংগীত হওয়ার উপযোগী। রবীন্দ্রনাথের ‘আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে’ গানে ‘বাংলাদেশ’ আছে, কিন্তু এই গানেরই অন্য দুটো বাক্য— ‘ও গো মা, তোমার কী মুরতি আজি দেখি রে’ এবং ‘তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে’। তাই, এই গানও ‘মুরতি’ আর ‘মন্দির’-এ মার খেয়ে যায়, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানজনগোষ্ঠীর ধর্মীয় ভাবধারার সাথে সংঘর্ষ বাধিয়ে ফেলে। ফলে, অজুহাত খুঁজতে চাইলে নানানভাবেই খোঁজা যাবে, শতভাগ বিতর্কমুক্ত বা সর্বজনগ্রহণযোগ্য কোনো জাতীয় সংগীত খুঁজে পাওয়া কস্মিনকালেও সম্ভব হবে না।
একটা মজার ব্যাপার এখানে উল্লেখ না-করলেই না। ‘আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে’ গানটা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৫ সালে। অর্থাৎ বাংলাদেশের জন্মের অন্তত ছেষট্টি বছর আগেই রবীন্দ্রনাথ ‘বাংলাদেশ’ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। এর আগে কেউ ‘বাংলাদেশ’ শব্দ ব্যবহার করেছেন, এমনটি অদ্যাবধি চোখে পড়েনি। বলাই বাহুল্য— ‘বাংলাদেশ’ নামক রাষ্ট্রের নামকরণ হয়েছে রবীন্দ্রনাথের এই গানের সূত্র ধরেই। রবীন্দ্রনাথে যাদের বিপুল ব্যারাম, তারা শেষমেশ ‘বাংলাদেশ’ নামও পালটাবেন কি না; এ-ব্যাপারে অবশ্য কোনো উচ্চবাচ্য শুনিনি। রবীন্দ্রনাথ এমনই এক মহাসমুদ্র; যার বুক থেকে কয়েক কলসি পানি তুলে তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলা যায়, কিন্তু পুরোটা সেচে ফেলা যায় না। সব নদীকে যেমন কোনো-না-কোনোভাবে সাগরে মিশতেই হয়, তেমনি ১৮৬১-পরবর্তী গোটা বাঙালি জাতিকেই রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে কিছু-না-কিছু ধার নিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ এমনই এক ব্যাংক, যার কাছে পুরো উপমহাদেশ এবং অবিভক্ত বাঙালি জাতি সরাসরি দায়বদ্ধ।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কেউ-কেউ বলছেন— জাতীয় সংগীত ‘আমার সোনার বাংলা’ই থাকুক, তবে এই গানের ‘মা’ শব্দটি পালটে অন্য কোনো শব্দ ব্যবহার করা হোক। তাদের কাছে এই গানের ‘মা’ হিন্দুয়ানির পরিচায়ক। মজার ব্যাপার হলো— ভারতের জাতীয় সংগীতেরও একটি শব্দ পরিবর্তনের জন্য দাবি উঠেছে বিভিন্ন সময়ে। ভারতের জাতীয় সংগীতের প্রথম পঙ্ক্তির পরপরই চলে আসে— ‘পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট, মারাঠা, দ্রাবিড়, উৎকল, বঙ্গ; বিন্ধ্য, হিমাচল, যমুনা, গঙ্গা— উচ্ছল জলধিতরঙ্গ।’ কিন্তু গানটি লেখার সময়ে (১৯১১) ‘সিন্ধু’ ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত থাকলেও দেশভাগের পর তা পাকিস্তানের অধীনে চলে যায়। তাই, ‘সিন্ধু’ শব্দটিকে পালটে ‘কাশ্মীর’ শব্দটি যোগ করার দাবি ওঠে ২০০৫ সালে। এই দাবির বিরোধীরা পালটা-যুক্তি দেন— জাতীয় সংগীতে ‘সিন্ধু’ শব্দটি কেবল ‘সিন্ধু প্রদেশ’ নয়, বরং সিন্ধু নদ ও ভারতীয় সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ সিন্ধি ভাষা ও সংস্কৃতিরও পরিচায়ক। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট এই যুক্তি মেনে নিয়ে জাতীয় সংগীতের ভাষায় কোনোরূপ পরিবর্তনের বিপক্ষে মত দেয় এবং সাফ জানিয়ে দেয়— রবীন্দ্রনাথের লেখায় কোনো কাটাছেঁড়া চলবে না।
২০১৮ সালে, আবারও, জাতীয় সংগীত থেকে ‘সিন্ধু’ শব্দটি বাদ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন আসাম রাজ্যসভার কংগ্রেস-দলীয় এক সদস্য; নাম— রিপুন বোরা। সিন্ধুর জায়গায় তিনি ‘উত্তর-পূর্ব’ ব্যবহারের দাবি জানান। কিন্তু রিপুন নামের এই ছন্দজ্ঞানহীন ব্যক্তিটি জানেনই না— ‘সিন্ধু’ শব্দ দুই মাত্রার আর ‘উত্তর-পূর্ব’ চার মাত্রার। দুই মাত্রার একটি শব্দ অপসারণ করে চার মাত্রার শব্দ বসালে তা যে আর গাওয়া যাবে না, দাঁতের মাঢ়ি খুলে পড়ে যাবে— এইটুকু বোধ তার নেই। মোদ্দা কথা— রবীন্দ্রনাথকে রেখে দেওয়া যায়, বাদ দেওয়া যায়; কিন্তু রবীন্দ্রনাথে অস্ত্রোপচার চলে না।
উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকরা পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের বিরুদ্ধে হঠকারিতার আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং একুশে ফেব্রুয়ারি ছাত্রজনতার বুকে গুলি চালিয়ে উর্দুর বিপরীতে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে উসকে দিয়েছিলেন। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবর্ষ উদ্যাপনে বাধা দিয়ে এবং রেডিও-টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন নিষিদ্ধ করে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালি জাতীয়তাবাদকে আরো শক্তিশালীভাবে আবির্ভূত হওয়ার ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বাঙালি জাতীয়তাবাদের শক্ত প্রতিচ্ছবি এবং তার রচিত ‘আমার সোনার বাংলা’ও এখন থেকে একশো উনিশ বছর আগে বাঙালি জাতীয়তাবাদ ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত একটি ঐতিহাসিক গান। বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী বিপ্লবীরা এই গানকে জাতীয় সংগীত হিসেবে ব্যবহার শুরু করেছেন দেশ স্বাধীন হওয়ার আগেই। তাই, এই গানকে জাতীয় সংগীত থেকে সরিয়ে দেওয়ার অর্থ হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামের ধারাবাহিকতার সুতো কেটে দেওয়া, স্বাধীনতাসংগ্রামীদের আবেগ-অনুভূতিকে কবরস্থ করা, মুক্তিযুদ্ধকালীন অস্থায়ী সরকারকে অস্বীকার করা, স্বাধীনতাবিরোধী সম্প্রদায় ও তাদের উত্তরসূরিদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিজয় নিশ্চিত করা।
শেখ মুজিবুর রহমানের সপরিবার মৃত্যুর পর জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের চেষ্টা হয়েছে অসংখ্যবার। সেসব চেষ্টার একটিও সফল হয়নি। স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে সুতীব্র গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে পতন হয়েছে স্বৈরশাসক শেখ হাসিনার। হাসিনার মহাপলায়নের পর জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের সুর তুলেছেন গোলাম আজমের ব্রিগেডিয়ার পুত্র। মনে রাখতে হবে— ‘আমার সোনার বাংলা’ শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, পৈত্রিক সম্পত্তিও নয়; এই গানকে শেখ হাসিনাও জাতীয় সংগীত বানাননি, তার পিতার একক ইচ্ছেয়ও এই গান জাতীয় সংগীত হয়নি। ‘আমার সোনার বাংলা’ জাতীয় সংগীত হয়েছে একটি নিরবচ্ছিন্ন, ধারাবাহিক ও ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। এই নিরবচ্ছিন্নতাকে বিচ্ছিন্ন করার, ধারাবাহিকতাকে অধারাবাহিক করার কিংবা ঐতিহাসিকতাকে ইতিহাসচ্যুত করার কোনো অবকাশ নেই। বাংলাদেশের জন্ম যারা চায়নি, ‘আমার সোনার বাংলা’র ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক শক্তি তাদের সম্মিলিত বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তির চেয়ে যোজন-যোজন বেশি।